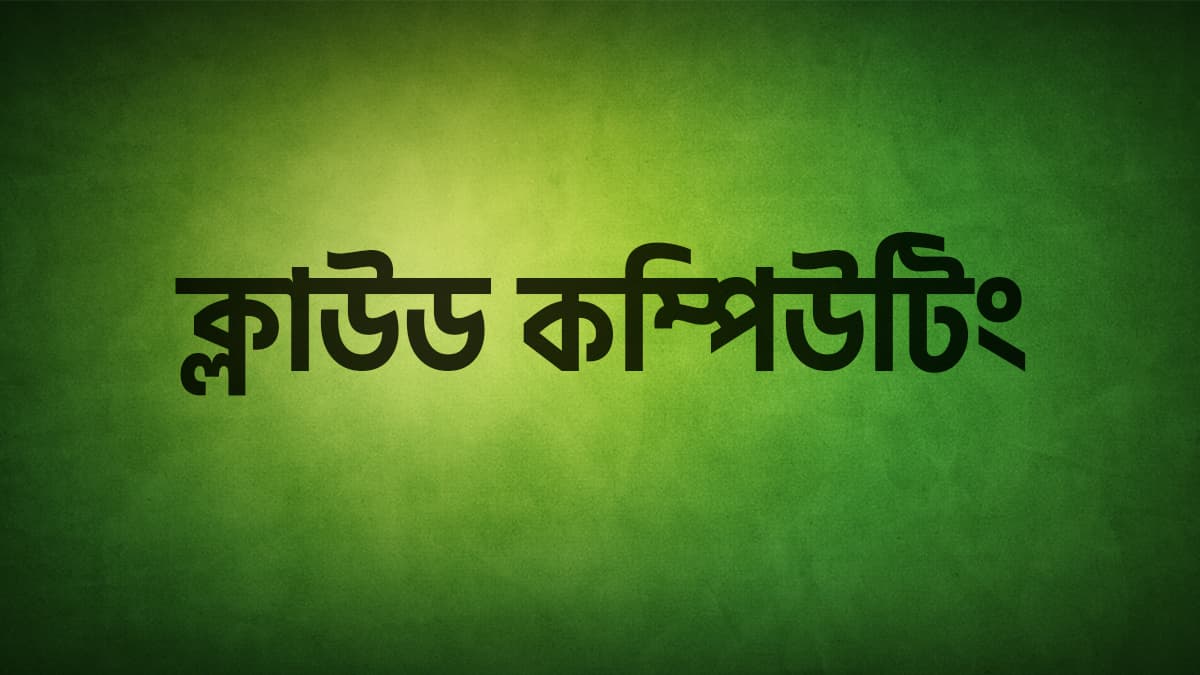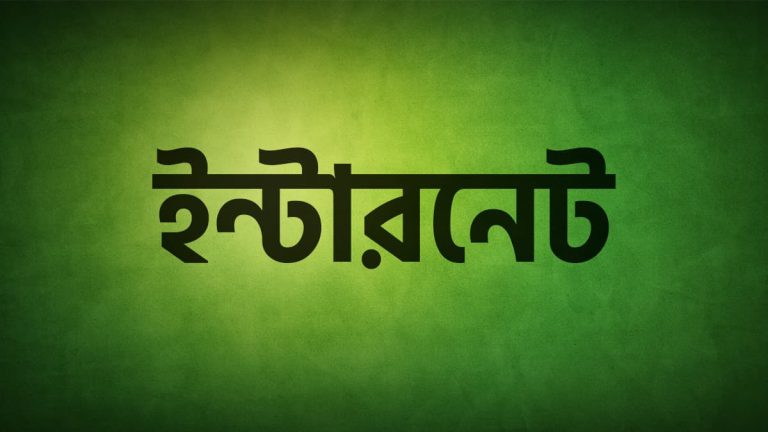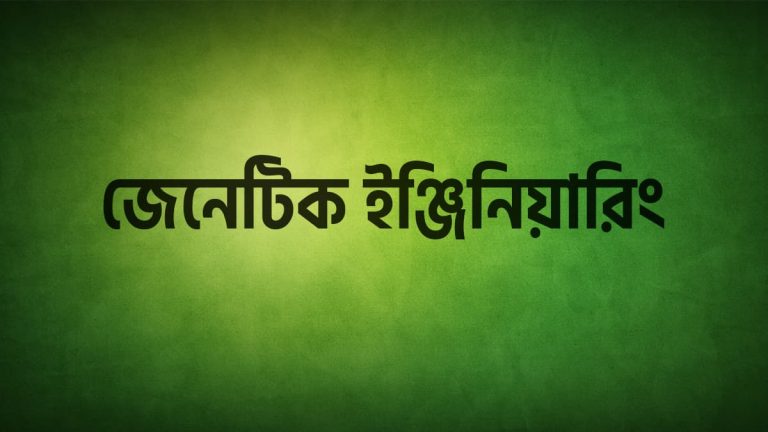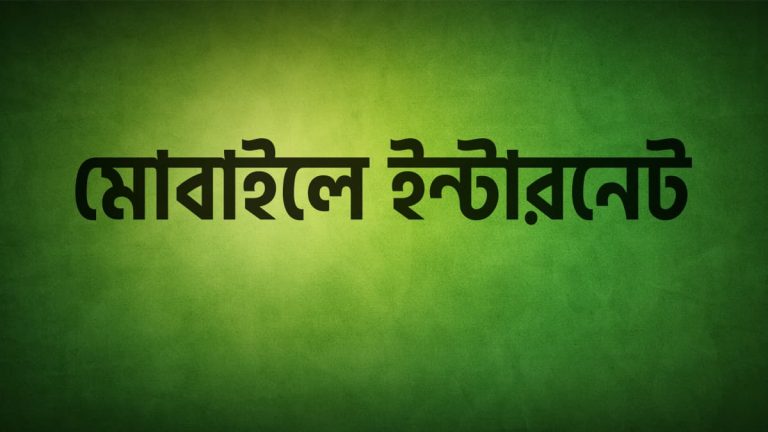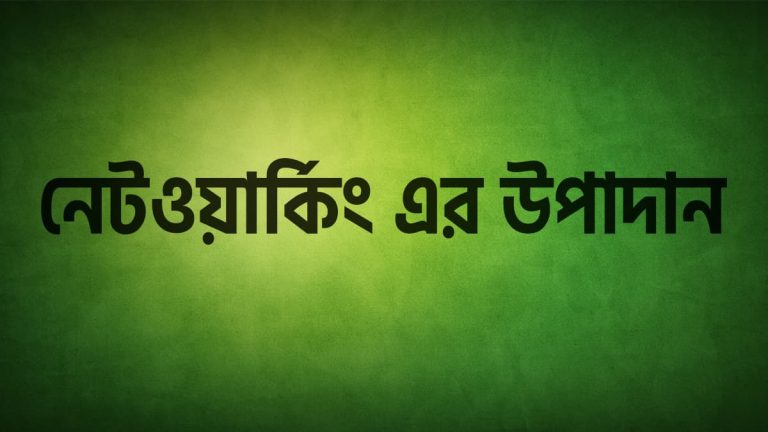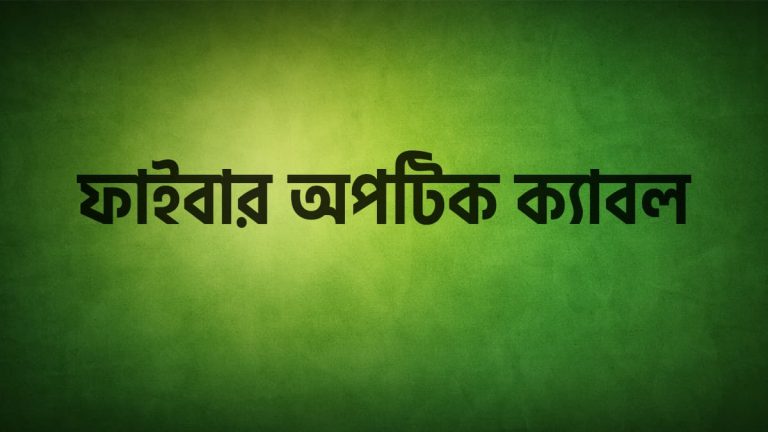ক্লাউড কম্পিউটিং যেভাবে আমাদের জীবন সহজ করেছে, ইতিহাস সহ
ধরা যাক, তোমাদের ঘরে ২০ জনের খাবার রান্না করার মতো হাঁড়ি-পাতিল এবং খাবার খাওয়ার জন্য থালা-বাসন এবং বসার জন্য চেয়ার-টেবিল রয়েছে। তোমাদের বাসায় ১৫০ জন মেহমান আসবে। এজন্য তোমরা কি বাকি ১৩০ জনের জন্য হাঁড়ি-পাতিল, ১৩০ টি থালা এবং ১৩০ টি চেয়ার কিনবে? এতগুলো জিনিস কেনার জন্য অনেক টাকা প্রয়োজন। এছাড়া এগুলো রাখার জন্য অনেক জায়গা প্রয়োজন।
এক্ষেত্রে অত টাকা খরচ না করে নিকটস্থ কোনো ডেকোরেটর থেকে এসব জিনিস যত সময়ের জন্য দরকার তত সময়ের জন্য ভাড়ায় আনা হয়। এতে করে নিজের প্রয়োজনও মিটে এবং অনেক টাকা খরচও বেঁচে যায়। ঠিক তদ্রুপ প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ফি-এর বিনিময়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা যায়। এ পদ্ধতিকে ক্লাউড কম্পিউটিং বলা হয়।
সূচিপত্র-
ক্লাউড কম্পিউটিং কি
ক্লাউড শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইন্টারনেটনির্ভর কম্পিউটিং হচ্ছে ক্লাউড কম্পিউটিং। ক্লাউড কম্পিউটিং এমন একটি কম্পিউটিং প্রযুক্তি, যা ইন্টারনেট ও কেন্দ্রীয় রিমোট সার্ভার ব্যবহারের মাধ্যমে ডেটা ও অ্যাপ্লিকেশনসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম। এতে ওয়েবে সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যবহারকারীকে ক্লায়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
ধরা যাক, একটি কোম্পানির ছয়টি সার্ভার দরকার। এগুলো ক্রয় করে সেটআপ করা এবং মেইনটেনেন্স করতে অনেক খরচ হবে। সবসময় এগুলোর ব্যবহার না হলেও খরচ কমানো যাবে না। কিন্তু কোম্পানিটি যদি ক্লাউড কম্পিউটিং সুবিধা নেয় (আমাজন ডট কমের ক্লাউডে m1.medium মেশিন ভাড়া নেয়) তাহলে ঘণ্টা হিসেবে বিল দিতে হলে খরচ অনেক কম হবে। যতক্ষণ ব্যবহার করা হবে, ততক্ষণের বিল দিতে হবে।
পাওয়ারফুল মেশিন চালানোর জন্য অতিরিক্ত বিদ্যুৎ খরচ বা মেশিন রুম ঠান্ডা রাখার দরকার নেই। লো-কনফিগারেশনের কিছু মেশিন রাখলেই হবে, আর থাকতে হবে দ্রুতগতির ইন্টারনেট। অফিসের এ লো-পাওয়ার কম্পিউটারগুলো দিয়ে ক্লাউডের ভার্চুয়াল মেশিনগুলোকে এক্সেস করতে পারবে।
যেহেতু মেশিনগুলো আমাজনের সার্ভারে, তাই সেগুলোর মেইটেন্যান্সের ঝামেলা নেই, খরচও নেই। হার্ডডিস্কসহ বিভিন্ন ধরনের ফিজিক্যাল মেমোরি ডিভাইসের ডেটা আগুনে পুড়ে যাওয়া, নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রভৃতি ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত রাখতে ক্লাউড কম্পিউটিং একটি কার্যকর পদ্ধতি।
ক্লাউড কোনো নির্দিষ্ট প্রযুক্তি নয়, বরং এটা একটা ব্যবসায়িক মডেল। অর্থাৎ ক্লাউড কম্পিউটিং-এ বেশকিছু নতুন পুরোনো প্রযুক্তিকে বিশেষভাবে বাজারজাত করা হয় বা ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। যেসব ক্রেতার অল্পসময়ের জন্য কম্পিউটার দরকার বা তথ্য রাখার জায়গা দরকার, কিন্তু অল্প সময়ের জন্য কম্পিউটার কেনার পেছনে অজস্র টাকা খরচের ইচ্ছে নেই, তারা ক্লাউডের মাধ্যমে ক্লাউড সেবাদাতার কাছ থেকে কম্পিউটার বা স্টোরেজ স্পেস ভাড়া নেন।
ক্লাউড কম্পিউটিং এর মডেল
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং (NIST) অনুসারে ক্লাউড কম্পিউটিং এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ: ক্লাউড কম্পিউটিং হলো ক্রেতার তথ্য ও বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনকে কোনো সেবাদাতার সিস্টেমে আউটসোর্স করার এমন একটি মডেল, যাতে ৩টি বৈশিষ্ট্য থাকবে-
Resource Flexibility / Scalability (যত চাহিদা তত সার্ভিস): ক্রেতা যত চাইবে, সেবাদাতা ততই অধিক পরিমাণে সেবা দিতে পারবে।
On Demand (যখন চাহিদা তখন সার্ভিস): ক্রেতা যখন চাইবে, তখনই সেবা দিতে পারবে। ক্রেতা তার ইচ্ছায় যখন খুশি তার চাহিদা বাড়াতে-কমাতে পারবে।
Pay as you go (যখন ব্যবহার তখন মূল্যশোধ): ক্রেতাকে আগে থেকে কোনো সার্ভিস রিজার্ভ করতে হবে না। ক্রেতা যা ব্যবহার করবে, তার জন্যই কেবল পয়সা দিতে হবে।
তাহলে এক বাক্যে বলা যায়- কম্পিউটার ও ডেটা স্টোরেজ সহজে, ক্রেতার সুবিধামতো চাহিবামাত্র এবং ব্যবহার অনুযায়ী ভাড়া দেয়ার সিস্টেমই হলো ক্লাউড কম্পিউটিং। ক্লাউড কম্পিউটিং-এর ক্ষেত্রে ক্রেতারা সাধারণত ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডারের ক্লাউডের সাথে যুক্ত হন। নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম আঁকার সময়ে ক্রেতা ও সার্ভারের মাঝের ইন্টারনেটের অংশটিকে অনেক আগে থেকেই মেঘের ছবি দিয়ে বোঝানো হতো। সে থেকেই ক্লাউড কম্পিউটিং কথাটি এসেছে।
ক্লাউড কম্পিউটিং-এর ইতিহাস
১৯৬০ সালে জন ম্যাক ক্যার্থি ক্লাউড কম্পিউটিং সম্পর্কে মতামত দেন এভাবে, “কম্পিউটেশন একদিন সংগঠিত হবে পাবলিক ইউটিলিটি হিসেবে।” তবে প্রকৃতপক্ষে এ ধারণা ভিত্তি লাভ করেছে ১৯৯০ সালের দিকে। নব্বই-এর দশকের শেষে বড় বড় কোম্পানি ইন্টারনেটে ব্যবসার আশায় বিশাল বিনিয়োগ করে ডেটা সেন্টার আর নেটওয়ার্কে।
২০০০ সাল নাগাদ হঠাৎ করে পুরা ব্যবসাটাই ধসে যায়, ফলে অনেকে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। তাদের ডেটা সেন্টারের মাত্র ৫% এর মতো ব্যবহৃত হচ্ছিল এবং বাকিটা সময়ে সিস্টেম অলস হয়ে বসে থাকতো। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া দিয়ে অলস বসে থাকা কম্পিউটারগুলোকে কাজে লাগানোর বুদ্ধি থেকেই শুরু হয় ক্লাউড কম্পিউটিং যুগের।
২০০৫ সাল থেকে আমাজন ডট কম ইলাস্টিক কম্পিউট ক্লাউড বা EC2 শুরু করে। এর পর আর পেছনে তাকাতে হয় নি ক্লাউড কম্পিউটিংকে। আইবিএম, মাইক্রোসফ্ট, গুগল থেকে শুরু করে প্রচুর কোম্পানি এখন ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবসার সাথে জড়িত।
ক্লাউডের প্রকারভেদ
ক্লাউডের ব্যবহারকারী কারা, তার ওপরে ভিত্তি করে ক্লাউড কম্পিউটিং পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে এগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো।
পাবলিক ক্লাউড (Public Cloud)
পাবলিক ক্লাউড হলো এমন ক্লাউড, যা সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত। যে টাকা দেবে, সেই সার্ভিস পাবে, এমন ক্লাউডকে বলা হয় পাবলিক ক্লাউড। যেমন- আমাজনের EC2। এসব ক্লাউডের সুবিধা হলো- যে কেউ এর সেবা নিতে পারে। আর অসুবিধাটা হলো- একই জায়গায় একাধিক ক্লায়েন্টের আনাগোনার ফলে নিরাপত্তার সমস্যা হতে পারে। Microsoft, Google প্রভৃতি পাবলিক ক্লাউডের অবকাঠামো স্থাপন ও পরিচালনা করার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস প্রদান করে থাকে।
প্রাইভেট ক্লাউড (Private Cloud)
প্রাইভেট ক্লাউডকে ক্লাউড বলা চলে কিনা এ নিয়ে মতভেদ আছে। এ রকম ক্লাউড হলো কোনো বড় সংস্থার নিজের নানা সার্ভিস চালাবার জন্য নিজের ডেটা সেন্টারকেই ক্লাউড মডেলে ব্যবহার করা। সমস্যা হলো, এতে করে কিন্তু খরচ অনেক হচ্ছে, নিজস্ব ডেটা সেন্টার বসাতে হচ্ছে, ম্যানেজ করার জন্য লোক রাখা হচ্ছে।
তবে বড় সংস্থার ক্ষেত্রে সুবিধাও আছে, কোনো বড় কোম্পানিতে ১০টি ডিপার্টমেন্ট থাকলে ১০টি ডেটা সেন্টার না বসিয়ে ১টিকেই ক্লাউড মডেলে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা যাচ্ছে। ধরা যাক, বাংলাদেশ সরকার তার নানা মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার ব্যবহারের খরচ কমাতে চায়। সেক্ষেত্রে একটা সরকারি প্রাইভেট ক্লাউড ভালো সমাধান হতে পারে।
হাইব্রিড ক্লাউড (Hybrid Cloud)
হাইব্রিড ক্লাউড হলো পাবলিক আর প্রাইভেটের সংমিশ্রণ। এখানে প্রাইভেট ক্লাউড দিয়ে প্রাথমিক চাহিদা মেটানো হয়, আর প্রাইভেট ক্লাউডের ধারণক্ষমতা অতিক্রান্ত হয়ে গেলে পাবলিক ক্লাউডের সাহায্য নেয়া হয়। পাবলিক ক্লাউডের চেয়ে হাইব্রিড ক্লাউডের খরচ বেশি, কারণ স্থানীয় স্থাপনা-তো বানাতেই হচ্ছে এখানে। তবে স্থানীয়ভাবে কাজ করিয়ে নেয়ার সুবিধাগুলো থাকছে, তার সাথে অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোরও একটা ব্যবস্থা এখানে থাকছে পাবলিক ক্লাউডে পাঠানোর মাধ্যমে।
ক্লাউডের মডেল (Model of Cloud Computing)
ক্লাউড কী সেবা দিচ্ছে, তার ভিত্তিতে ক্লাউডকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
- Infrastructure-as-a-Service (IaaS) বা অবকাঠামোগত সেবা
- Platform-as-a-Service (PaaS) বা প্লাটফর্মভিত্তিক সেবা
- Software-as-a-Service (SaaS) বা সফটওয়্যার সেবা
IaaS: Infrastructure-as-a-Service (অবকাঠামোগত সেবা)
অবকাঠামো ভাড়া দেয়ার সার্ভিস। যেমন, আমাজন ইলাস্টিক কম্পিউট ক্লাউড (EC2) এর উদাহরণ। EC2-তে ডেটা সেন্টারের প্রতি সার্ভারে ১ থেকে ৮টি ভার্চুয়াল মেশিন চলে, ক্লায়েন্টরা এগুলো ভাড়া নেন। ভার্চুয়াল মেশিনে নিজের ইচ্ছেমতো অপারেটিং সিস্টেম বসানো চলে। এতে সুবিধা হলো, সবকিছু ইউজার নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আর অসুবিধা হলো, সবকিছুর ব্যবস্থা ইউজারকে নিজেই করতে হয়।
PaaS: Platform-as-a-Service (প্লাটফর্মভিত্তিক সেবা)
এখানে সরাসরি ভার্চুয়াল মেশিন ভাড়া না দিয়ে ভাড়া দেয়া হয় প্লাটফর্ম, যার উপরে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারেন ইউজারেরা। যেমন- গুগলের অ্যাপ ইঞ্জিন উদাহরণ। এ সার্ভিস ব্যবহার করলে গুগল তাদের এপিআই ব্যবহার করতে দেবে, সেটার সুবিধা অ্যাপ্লিকেশন বানাতে পারবে। এ অ্যাপ্লিকেশন চলবে গুগলের ক্লাউডে। এছাড়া মাইক্রোসফটের Azure-ও এর অপর একটি উদাহরণ হতে পারে।
SaaS: Software-as-a-Service (সফটওয়্যার সেবা)
সফটওয়্যার অ্যাজ এ সার্ভিস হলো ক্লাউডভিত্তিক এমন একটা সেবা, যেখানে ইউজাররা ক্লাউডের উপরে চলছে এমন রেডিমেইড সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারবে। যেমন, Google Docs। গুগল ডক দিয়ে মাইক্রোসফট অফিসের প্রায় সব কাজই (ডকুমেন্ট, স্প্রেডশিট, প্রেজেন্টেশন) করা যায়।
ক্লাউড কম্পিউটিং-এর সুবিধা
ক্লাউড ব্যবহার করে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন-
অপারেটিং খরচ কমানো
ক্লাউড ব্যবহার করে অপারেটিং খরচ (Operating cost) যথেষ্ট পরিমাণ কমানো সম্ভব। ক্লাউডে স্টোরেজ নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। যখন যত দরকার, সুলভ মূল্যে তখন তত স্টোরেজ সুবিধা পাওয়া যাবে। এখানে প্রায় সীমাহীন স্টোরেজ সুবিধা রয়েছে।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফ্টওয়্যার আপডেট ও রক্ষণাবেক্ষণ
ক্লাউডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার আপডেট ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা থাকে বিধায় সার্ভিস গ্রহণকারী গ্রাহকের এসব বিষয় নিয়ে কেনো চিন্তা করতে হয় না।
খরচ কম সহজ প্রবেশাধিকার
ক্লাউডে রেজিস্ট্রিকৃত গ্রাহকরা তার ডেটাবেজে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোনো অবস্থান থেকে যে কোনো সময় ডেটা একসেস করতে পারে। ক্লাউড কম্পিউটিং-এর গ্রাহক সফ্টওয়্যার সার্ভিসসহ সার্ভিস নিলে প্রয়োজন অনুযায়ী সফটওয়্যারও সুলভে ব্যবহার করতে পারবে।
সহজপ্রাপ্যতা
ক্লাউড কম্পিউটিং-এর গ্রাহক তার প্রয়োজন অনুযায়ী সার্ভিস নিতে পারে। শুরুতে একটি সার্ভার ভাড়া নিয়ে প্রয়োজনে যে কোনো সময় একশটি সার্ভারও ভাড়া নিতে পারবে। ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে বিল দিতে হবে। কম ব্যবহার করলে কম বিল দিতে হবে।
নিরাপত্তা
ক্লাউড কম্পিউটিং সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কারিগরি দক্ষতা, ব্যাকআপ ক্যাপাসিটি অনেক বেশি। তাই কোনো ছোট প্রতিষ্ঠানের স্থাপিত নিজস্ব সেটআপের চেয়ে এগুলো বেশি নিরাপদ।
ছোট ও প্রাথমিক উদ্যোক্তাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ
একটি ছোট বা মাঝারি মানের প্রতিষ্ঠানের জন্য কয়েক লাখ টাকা দিয়ে একটি সার্ভার কেনা এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভালো বেতনে দক্ষ লোক রাখা, সফটওয়্যার কেনা কঠিন। ক্লাউড কম্পিউটিং-এ খরচ ও ঝামেলা অনেকাংশে কমিয়ে এনে সে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে
সাহায্য করতে পারে।
বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী/গবেষকদের সুবিধা
অনেকসময় বিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্য সাময়িকভাবে বিশাল কম্পিউটিং সুবিধা প্রয়োজন হয়, যা প্রতিষ্ঠা করা অনেক ব্যয়সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে ক্লাউড সুবিধা নিয়ে কাজ করতে পারে।
সহজ পরিবর্তন
প্রচলিত প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা কঠিন। কারণ এতে অনেক লোকবল ও অর্থনৈতিক বিষয় জড়িত থাকে। কিন্তু ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে এ ধরনের কোনো সমস্যা নেই।
ক্লাউড কম্পিউটিং-এর অসুবিধা
নিরাপত্তা: সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না বিধায় তথ্যের নিরাপত্তা তুলনামূলকভাবে কম।
সার্ভার ডাউন: মেইনটেন্যান্স বা হ্যাকিং অথবা অন্য কোনো কারণে সার্ভার ডাউন হলে সম্পূর্ণ কাজ বন্ধ হয়ে যায়।
ফি প্রদান: নির্ধারিত সময় অন্তর নির্ধারিত ফি দিতে হয়, না দিলে এ সার্ভিস বন্ধ করে দিলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়।
ব্যবহারকারীর নিয়ন্ত্রণ: প্রোগ্রাম বা অ্যাপ্লিকেশনের ওপর ব্যবহারকারীদের নিয়ন্ত্রণ কম থাকে বা থাকে না।
প্রশিক্ষণ: সাধারণত কর্মীদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়।
ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীলতা: যেহেতু এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ইন্টারনেটভিত্তিক, তাই ইন্টারনেট কানেকশনে কোনো সমস্যা হলে অথবা গতি স্লো হলে অনেক সমস্যা দেখা দেয়।
স্টোরেজ লিমিট: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্টোরেজের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকে।
স্লো স্পিড: বড় ফাইল আপলোড বা ডাউনলোড ধীর গতির হতে পারে।
ক্লাউড কম্পিউটিং আমাদের জীবন অনেক সহজ করেছে এবং আমাদের খরচ অনেক কমিয়ে দিয়েছে। আমাদের জীবনে ক্লাউড কম্পিউটিং এর বিকল্প নেই, তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম।