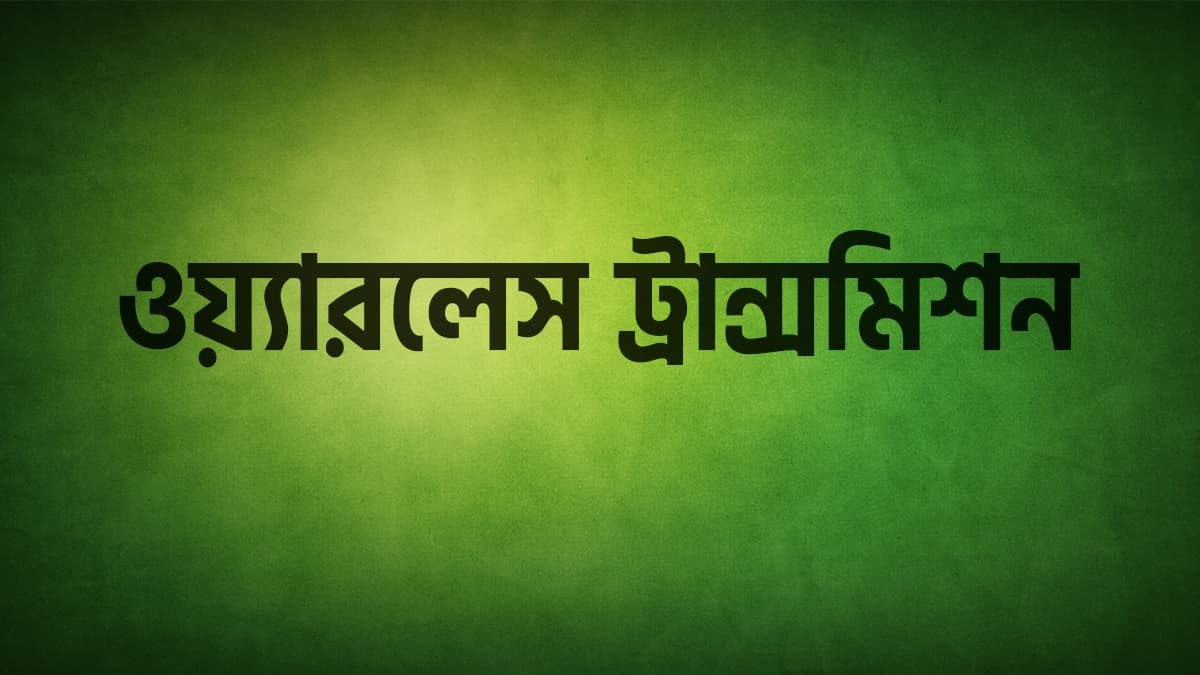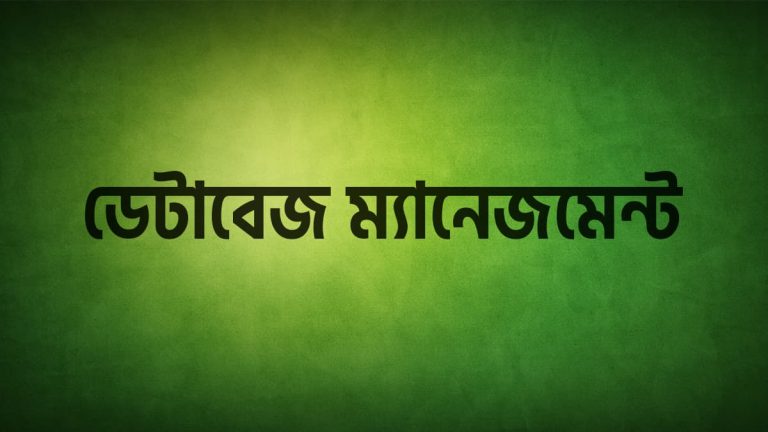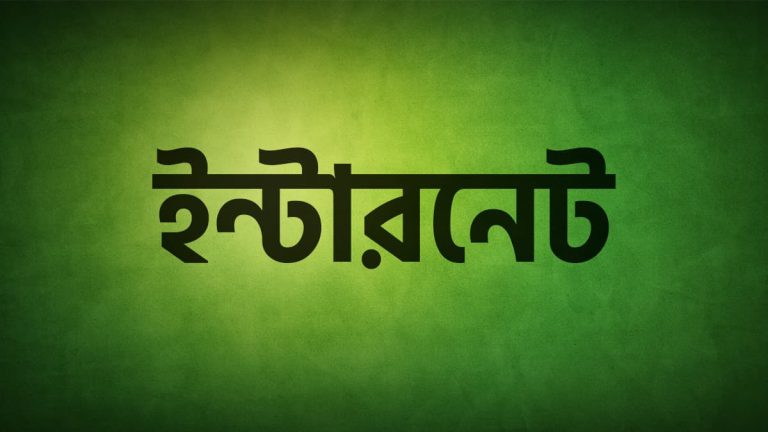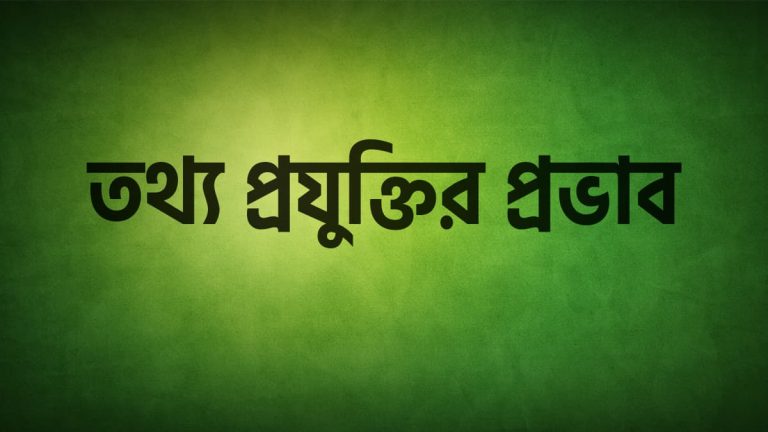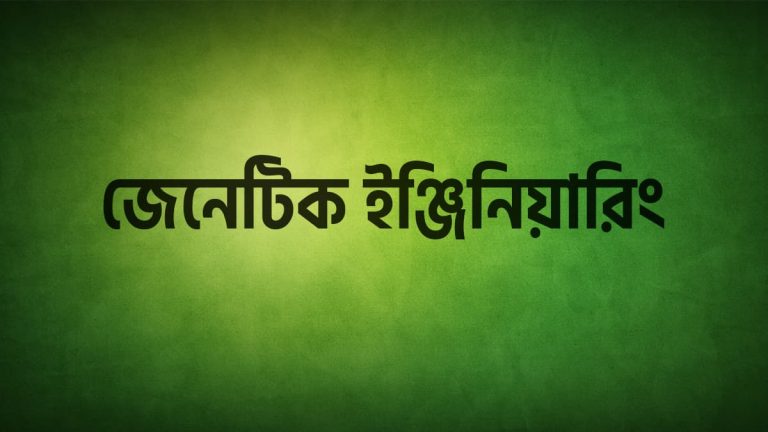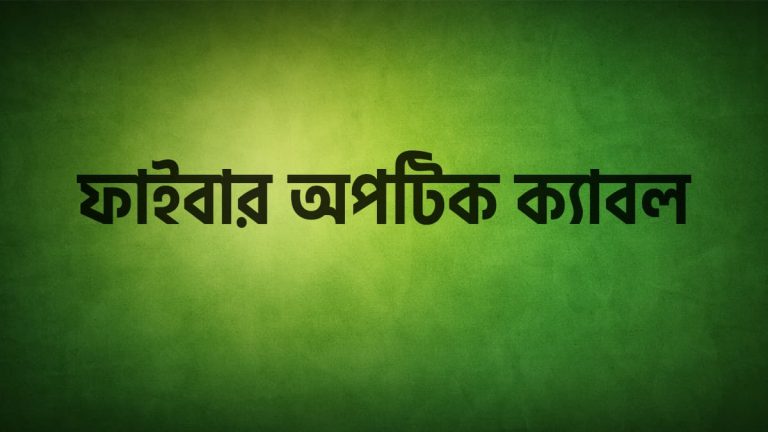ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন প্রযুক্তি, প্রকারভেদ ও ব্যবহার
বর্তমান সময়ে ওয়্যারলেস হলো সবচাইতে জনপ্রিয় একটি ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম। যে মাধ্যম দ্বারা কোনো প্রকার তার বা কন্ডাক্টরের এক নজরে বিভিন্ন ক্যাবলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার- বাহিকে সংযোগ ছাড়াই তড়িৎ চৌম্বকীয় সংকেত (Electromagnatic Signal) ব্যবহার করে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়, তাকে তারবিহীন মাধ্যম বা ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন মিডিয়া বলা হয়।
এক্ষেত্রে বায়ুতে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন বা তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের মাধ্যমে এই যোগাযোগ সংঘটিত হয়, যার ফ্রিকোয়েন্সি সীমা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম (Electromagnetic Spectrum) দ্বারা নির্ধারিত থাকে। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম হলো তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের রেঞ্জ বা ব্যাপ্তি, যেটি জুড়ে শূন্য বা বায়ু মাধ্যমে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন বা তরঙ্গ শক্তিটি অবস্থান করে।
এখানে ফ্রিকোয়েন্সি (প্রতি সেকেন্ডে কম্পন) যত কম হবে, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তত বেশি হবে। যেমন চিত্রে রেডিও ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি সবচেয়ে কম(101) হওয়ায় এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি (103)। আবার গামা রে-এর ফ্রিকোয়েন্সি সবচেয়ে বেশি (100) হওয়ায় এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম(10-12)। উল্লেখ্য, এই স্পেকট্রামের ক্ষুদ্র একটা অংশ দৃশ্যমান আলো হিসেবে দেখা যায়।
সূচিপত্র-
ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন এর প্রকারভেদ
তারবিহীন এই মাধ্যমে ডেটা তারযুক্ত মাধ্যমের মতো কোনো একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত না হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এজন্য ওয়্যারলেস মাধ্যমকে Unguided Media নামেও অভিহিত করা হয়। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের দুইটি ক্ষেত্র কমিউনিকেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো হলো-
- রেডিও ওয়েভ (Radio wave)
- মাইক্রোওয়েভ (Microwave)
- ইনফ্রারেড (Infrared)
রেডিও ওয়েভ (Radio wave)
কিলোহার্টজ (KHz) থেকে 300 গিগাহার্টজ (GHz)-এর মধ্যে সীমিত তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ (ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম)-কে রেডিও ওয়েভ বলা হয়। যদিও কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে কার্যত রেডিও ওয়েভের ব্যবহার 10 কিলোহার্জ থেকে 1 গিগাহার্জ ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায়) এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমা 30 সে.মি. থেকে 30 কি.মি পর্যন্ত বিস্তার করতে পারে।
রেডিও ওয়েভ হলো এক ধরনের ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন মিডিয়া, যা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (RF) সিগন্যালের মাধ্যমে ডেটা ট্রান্সমিট করে থাকে । অন্যান্য সব তড়িৎ-চৌম্বকীয় বিকিরণের মতো বেতার তরঙ্গও আলোর গতিতে ভ্রমণ করে। প্রাকৃতিক উপায়ে বেতার তরঙ্গ সৃষ্টি হয় সাধারণত বজ্রপাত বা মহাজাগতিক বস্তু থেকে।
কৃত্রিমভাবে তৈরিকৃত বেতার তরঙ্গ মোবাইল টেলিযোগাযোগ, বেতার যোগাযোগ, সম্প্রচার, রাডার ও অন্যান্য দিকনির্দেশনা (Navigation) ব্যবস্থা, কৃত্রিম উপগ্রহের সাথে যোগাযোগ, কম্পিউটার নেটওয়ার্কসহ অসংখ্য কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে রেডিও ওয়েভ ব্রডকাস্টের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়, কেননা এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি বিধায় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়।
রেডিও ওয়েভ কমিউনিকেশনকে ওয়াইড রেঞ্জ কমিউনিকেশন বা রেডিও ওয়েবভিত্তিক কমিউনিকেশনও বলা হয়। রেডিও ওয়েভ সিগন্যাল অনেক দূরের বা কাছের রেঞ্জে হতে পারে এবং বায়ুমণ্ডলে খুব বেশি শোষিত না হওয়া এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার কারণে পাহাড় বা বিল্ডিং বা অন্যান্য বাধা ভেদ করতে পারে।
বায়ুমণ্ডলের আয়োনোস্ফিয়ার থেকে প্রতিফলিত হয় বলে এটি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাঠানো সম্ভব। এর ব্যান্ডউইথ 64 kbps. এটি ICT-এর একটি শক্তিশালী মাধ্যম। রেডিও ওয়েভের জন্য ট্রান্সমিটার, রিসিভার, অ্যান্টেনা এবং উপযুক্ত টার্মিনাল যন্ত্রপাতি থাকতে হয়।. ওয়েভ পাঠানোর জন্য যে অ্যান্টেনার প্রয়োজন হয়, তার দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আনুমানিক চারভাগের এক ভাগ হতে হয়।
রেডিও ওয়েভ যেভাবে পৃথিবীর উপরিভাগে (ট্রান্সমিটার থেকে রিসিভার পর্যন্ত) শূন্যস্থানের মধ্যে পরিভ্রমণ করে এবং যেভাবে তার পরিবাহক মাধ্যমের সাথে মিথষ্ক্রিয়া করে থাকে, তাকে রেডিও ওয়েভ প্রোপাগেশন (Propagation) বলে। এটি বাস্তব রেডিও কমিউনিকেশন সিস্টেম ডিজাইনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।
বিভিন্ন পরিবেশে রেডিও ওয়েভ বিকিরিত হবার সময় প্রতিফলন, প্রতিসরণ, পোলারাইজেশন, ডিফ্র্যাকশন ইত্যাদি অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভিন্ন কম্পাঙ্কের (Frequency) বেতার তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন রকম হয় এবং এর ওপর ভিত্তি করে এএম, এফএম প্রভৃতি বিভিন্ন রেডিও ব্যান্ড সম্প্রচারিত হয়।
রেডিও ওয়েভ ব্যবহারের সুবিধা
১. রেডিও তরঙ্গ বিল্ডিং, পাহাড়-পর্বত, যানবাহনসহ যে কোনো বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম। তাই এক্ষেত্রে লাইন অব সাইট কোনো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় না।
২. রেডিও তরঙ্গ বায়ুমণ্ডলের আয়োনোস্ফিয়ার পর্যন্ত বিস্তার করতে পারে বিধায় এর দ্বারা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যায় ।
৩. রেডিও তরঙ্গ সহজেই বায়ুমণ্ডল দ্বারা শোষিত হয় না বিধায় এই মাধ্যমে ইন্টারফিয়ারেন্স তুলনামূলকভাবে কম হয়।
রেডিও ওয়েভ ব্যবহারের অসুবিধা
১. রেডিও তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি কম হওয়ায় এটি একসাথে বেশি ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে না।
২. রেডিও তরঙ্গের অতিমাত্রায় বিকিরণ মানুষের শরীর ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে।
মাইক্রোওয়েভ (Microwave)
ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের ৩০০ মেগাহার্জ (MHz) থেকে ৩০০ গিগাহার্জ (GHz) পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডকে মাইক্রোওয়েভ বলা হয়। অনেকের মতে, 1 GHz হতে 100 GHz-এর ভেতরে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডকে মাইক্রোওয়েভ বলা হয়।
এটি হলো একটি হাই-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও ওয়েভ। মাইক্রোওয়েভ সাধারণভাবে 2 গিগাহার্জ বা তার অধিক ফ্রিকোয়েন্সিতে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে। দূরপাল্লায় ডেটা ট্রান্সমিশন-এ মাইক্রোওয়েভ অত্যন্ত জনপ্রিয় পদ্ধতি।
মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম মূলত দু’টো ট্রান্সসিভার (Transceiver) নিয়ে গঠিত। এর একটি সিগন্যাল ট্রান্সমিট (Transmit) এবং অন্যটি রিসিভ (Receive) করে। দুটি ট্রান্সসিভার-এর মাঝে মাইক্রোওয়েভের এন্টিনা (Antenna) থাকে, যাতে সিগন্যাল বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে এবং পথিমধ্যে কোনো বস্তু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে। মাইক্রোওয়েভ বাঁকাপথে চলাচল করতে পারে না এবং প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে কোনো বাধা থাকলে ডেটা স্থানান্তর সম্ভব হয় না।
মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ দু’ধরনের হতে পারে-
- ক. টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ
- খ. স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ
ক. টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোয়েভ
এ প্রযুক্তিতে ভূ-পৃষ্ঠেই ট্রান্সমিটার ও রিসিভার বসানো হয়। এতে মেগাহার্জ সীমার নিচের দিকে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হয়। ট্রান্সমিটার ও রিসিভার মুখোমুখী (LOS- Line Of Sight) যোগাযোগ করে থাকে এবং সিগন্যাল বাধা অতিক্রম করতে পারে না এবং বক্রপথে যেতে পারে না।
যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন করার জন্য সাধারণত বড় টাওয়ার, উঁচু ভবন বা পাহাড়ে টেরিস্ট্রিয়াল ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার বসানো হয়। তরঙ্গের সিগন্যাল ঠিক রাখার জন্য ৪০ কি.মি থেকে ৫০ কি.মি পর পর রিপিটার বা রিলে স্টেশন স্থাপন করতে হয়। স্বল্প দূরত্বের মধ্যে অধিক ফ্রিকোয়েন্সিতে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয়।
খ. স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ
মাইক্রোওয়েভ বায়ুমণ্ডলের আয়নোস্ফিয়ার স্তর ভেদ করে যেতে বা আসতে পারে বলে কৃত্রিম উপগ্রহের সহায়তায় মাইক্রোওয়েভে সিগন্যাল আদান-প্রদান করা শুরু হয়। রকেটের মাধ্যমে স্যাটেলাইটকে পৃথিবী থেকে ২২,২৩৬ মাইল (৩৫,৭৮৬ কি.মি.) উপরে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জিওস্টেশনারি অরবিটে স্থাপন করা হয়। যেখানে ক্যাবলের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব নয়, সেখানে স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন ব্যবহৃত হয়।
স্যাটেলাইটে ট্রান্সমিটার, রিসিভার, শক্তিশালী রিসিভার ট্রান্সমিটার অ্যান্টেনা VSAT (Very Small Aperture Terminal), সোলার পাওয়ার থাকতে হয়। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে খুব তাড়াতাড়ি কম খরচে যোগাযোগ করা যায়। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর বিশ্বময় সরাসরি সম্প্রচার, আন্তঃমহাদেশীয় দূরবর্তী টেলিফোন কল করা এবং ইন্টারনেটে সিগন্যাল পাঠানোর জন্য স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।
অধিক দূরত্বে অনেক বেশি পরিমাণ ডেটাকে পরিবহণের জন্য স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ অপরিহার্য। স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশনের জন্য ভূমিতে আকাশমুখী করে ডিশ অ্যান্টেনার মতো একটি অ্যান্টেনা স্থাপন করা হয়। এটিকে ভিস্যাট বলা হয়। মাটিতে স্থাপিত বেজ স্টেশন বা ভিস্যাটগুলোকে ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র বলা হয়।
ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্ৰ হতে ভিস্যাটগুলো মাইক্রোওয়েভ ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে সরাসরি স্যাটেলাইটে তথ্য পাঠায়। এই ফ্রিকোয়েন্সির পরিমাণ হলো 6 GHz। এরপর স্যাটেলাইট (কৃত্রিম উপগ্রহ)-এ থাকা ট্রান্সপন্ডেন্ট দ্বারা ঐ মাইক্রোওয়েভ সিগন্যাল আরও বেশি বিবর্ধিত বা অ্যামপ্লিফাই করে সেটিকে রিলে করা হয়। এর ফ্রিকোয়েন্সি হয় 4GHz।
টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভে রিপিটার যে ভূমিকা পালন করে, স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে ট্রান্সপন্ডেন্ট সেই ভূমিকা পালন করে। পুনরায় ভূমিতে থাকা বিভিন্ন ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রগুলো ঐ বিবর্ধিত সিগন্যালগুলোকে গ্রহণ করে যথাস্থানে প্রেরণ করে।
যেহেতু মাইক্রোওয়েভ মুখোমুখী সংযোগ বা লাইন অব সাইট মেইনটেইন করে, এজন্য ভূমিতে স্থাপিত ভিস্যাটকে আকাশমুখী করে স্থাপন করা হয়। স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভের সিগন্যাল ট্রান্সমিশনের প্রতিবন্ধকতাগুলো হলো বাতাসে থাকা বিভিন্ন গ্যাস, জলীয় বাষ্প, আয়নোস্ফিয়ার প্রভৃতি। এগুলো মাইক্রোওয়েভ সিগন্যালকে শোষণ করে।
স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ এর ব্যবহার
- পৃথিবীর জলবায়ু এবং আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করার কাজে
- টেলিভিশন সম্প্রচার কাজে
- অপেশাদার রেডিও যোগাযোগের ক্ষেত্রে
- প্রতিরক্ষা কাজে
- ইন্টারনেট যোগাযোগের ক্ষেত্রে
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে
- দূরের গ্রহ, গ্যালাক্সি ও মহাশূন্যের বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ কাজে
- গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (Global Positioning System-GPS)-এর মতো বিভিন্ন অবস্থান নির্ণয় কাজে
স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ এর সুবিধা
১. বিপুল পরিমাণ ডেটা আদান-প্রদান করা সম্ভব।
২. পৃথিবীর একপ্রান্তে বসবাসকারী লোকজন অন্যপ্রান্তে বসবাসকারী লোকজনের কাছাকাছি থাকতে পারে।
৩. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
৪. প্রাকৃতিক বিপর্যয়কালে যখন সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে, তখন স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।
৫. আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব।
৬. ভয়েস কলিং, ভিডিও কলিং, রেডিও, টেলিভিশন চ্যানেল, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স ইত্যাদি সেবা পাওয়া যায়।
৭. একটি মূল্য সাশ্রয়ী ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে লং ডিসটেন্স কল করা যায়।
স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ এর অসুবিধা
১. স্যাটেলাইট পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে হওয়ায় সেখানে সিগন্যাল পাঠাতে অনেক বড় এন্টেনার প্রয়োজন হয়।
২. স্যাটেলাইট প্রযুক্তিটির বাস্তবায়ন ও তদারকির বিষয়টি ব্যয়বহুল।
৩. স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে সিগন্যাল ডিলে একটি অসুবিধা হিসেবে আবির্ভূত হয়।
৪. ভ্রমণরত অবস্থায়, খারাপ আবহাওয়ায় কিংবা সানস্পট-এর কারণে বিভিন্ন সেবা বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
৫. ডেটার অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।
ইনফ্রারেড (Infrared)
বাসা-বাড়িতে টেলিভিশন, ভিসিডি প্লেয়ার, খেলনা গাড়ি, এয়ারকন্ডিশন প্রভৃতি চালানোর জন্য রিমোট, কন্ট্রোল ব্যবহার করা হয়। রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে মূল ডিভাইসকে এক্ষেত্রে কোন তারবিহীন মাধ্যম দ্বারা যোগাযোগ করা হয়। এটি হলো ইনফ্রারেড নামের একধরনের তরঙ্গনির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা।
ইনফ্রারেড হলো একধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, যার ফ্রিকোয়েন্সি সীমা টেরাহার্জ (THz) হয়ে থাকে। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামে 300 গিগাহার্জ (GHz) হতে 430 টেরাহার্জ (THz) পর্যন্ত বিস্তৃত ব্যান্ডকে ইনফ্রারেড নামে অভিহিত করা হয়। খুবই কাছাকাছি ডিভাইসের মধ্যে ডেটা।
কমিউনিকেশনে ইনফ্রারেড ব্যবহার করা হয়। ১৮০০ শতাব্দীতে উইলিয়াম হার্শেল এ তরঙ্গ আবিষ্কার করেন, যার অবস্থান ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামে মাইক্রোওয়েভ ও দৃশ্যমান আলোর মাঝামাঝি। এ প্রযুক্তিতে দু’প্রান্তে ট্রান্সমিটার ও রিসিভার থাকে।
সিগন্যাল ট্রান্সমিট করার কাজটি LED (Light Emitting Diode)-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং ফটো ডায়োড সিগন্যাল রিসিভ বা গ্রহণ করে। ইনফ্রারেড সিগন্যালের অসুবিধা হলো এটি ঘরের দেয়াল বা শক্ত বস্তু ভেদ করে অপরপ্রান্তে যেতে পারে না।
ইনফ্রারেড-এর বৈশিষ্ট্য
- দৃশ্যমান আলোর চেয়ে বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্য (700nm-1mm)
- ফ্রিকোয়েন্সি লেভেল 300GHz – 430THz
- ডেটা চলাচলের গতি তার মাধ্যমের তুলনায় কম
ইনফ্রারেড-এর ব্যবহার
- গৃহসামগ্রী পরিচালনা যেমন- ঘরের দরজা, জানালা, পর্দা, লাইট, ফ্যান, এসি
- প্রভৃতি রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে চালু বা বন্ধ করতে
- কার লকিং সিস্টেমে
ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন বা, তারবিহীন মাধ্যম নিয়ে এই ছিলো আমাদের আজকের লেখা, কোন কিছু বাদ পড়লে কমেন্টে জানাবেন। আমরা পরবর্তী সংস্করণে যুক্ত করে দিব।